শুক্রবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৫ ফাল্গুন ১৪৩২
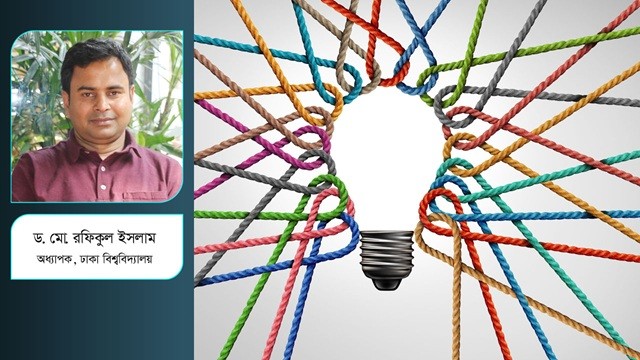
ছবি সংগৃহীত
জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (SDGs) একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে—একটি সমাজ যেখানে কেউ পিছিয়ে থাকবে না, বরং সব নাগরিক সমান মর্যাদা, অধিকার ও সুযোগ পাবে।
বিশেষভাবে, লক্ষ্য ১০ (SDG 10) বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে ও দেশগুলোর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানায়। এই অন্তর্ভুক্তি যেন বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, জাতিসত্তা, ধর্ম, ভাষা বা যেকোনো সামাজিক পটভূমির ভিত্তিতে কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয়।
উন্নয়ন অর্থনীতিবিদগণ দীর্ঘদিন ধরেই এই অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের পক্ষে যুক্তি দিয়ে আসছেন। নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন (Amartya Sen) তার ‘সক্ষমতা পন্থা’ (Capability Approach)-এ বলেন, প্রকৃত উন্নয়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের স্বাধীনতা ও বিকাশের সুযোগ প্রসারিত করে।
তিনি বলেন, উন্নয়নের মানদণ্ড হওয়া উচিত মানুষের জীবনের প্রকৃত বিকাশ—তারা কী করতে ও কী হতে পারছে তার ওপর ভিত্তি করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন দরিদ্র শিক্ষার্থী যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে না পারেন বা একজন সংখ্যালঘু যদি স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, তাহলে শুধু জিডিপি বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়—এই পরিস্থিতি উন্নয়নের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।
একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের মানে হলো এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে প্রত্যেকে—বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারীরা, আদিবাসী সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী মানুষ, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু—সমান সুযোগ ও মর্যাদা নিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ, ব্রাজিল বা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সরাসরি নগদ সহায়তা (conditional cash transfers) বা শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ওপর বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের কার্যকর দৃষ্টান্ত।
এমন সমাজ গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দিকও রয়েছে। দারন আসেমোগলু ও জেমস এ রবিনসন (Daron Acemoglu and James A. Robinson) তাদের আলোচিত গ্রন্থ ‘Why Nations Fail’-এ বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান—যেগুলো ক্ষমতা ও সম্পদের বণ্টনে ন্যায়পরায়ণ ও অংশগ্রহণমূলক—দীর্ঘমেয়াদে একটি দেশের উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করে। অপরদিকে, নিষ্কাষণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাখে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে প্রান্তিক করে তোলে, যা উন্নয়নকে স্থবির করে দেয়।
তবে প্রশ্ন থেকে যায়—একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ কীভাবে প্রতিষ্ঠা সম্ভব? এর উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যায়, সমাজে সহানুভূতিশীল ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন নেতৃত্বের প্রয়োজন। এতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, শিক্ষক, চিন্তাবিদ, ধর্মীয় নেতা, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।
শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, পাঠ্যসূচিতে বহুত্ববাদ ও সমানাধিকারের মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যেমন, কানাডার শিক্ষানীতিতে বহুসাংস্কৃতিকতা ও আদিবাসী ইতিহাস শেখানো হয়, যা সমাজে সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলে।
অপরদিকে, নীতিনির্ধারকদের উচিত এমন নীতি গ্রহণ করা যা সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণি—বিশেষ করে দুর্বল ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও অধিকার অগ্রাধিকার দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের ‘মনরেগা’ কর্মসূচি গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে তাদের সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার একটি কৌশল হিসেবে কাজ করছে। একইভাবে, ধর্মীয় নেতা ও গণমাধ্যমকে হতে হবে শান্তি, সহনশীলতা ও মানবিক সহাবস্থানের পক্ষে সোচ্চার—যাতে সমাজে বিভাজন নয়, বরং সংহতি ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
বাংলাদেশের প্রসঙ্গে এলে দেখা যায়, দেশটি একদিকে যেমন ঘনবসতিপূর্ণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি রাষ্ট্র, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের পথে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। জাতিসংঘের SDG অনুযায়ী ‘কেউ পিছিয়ে থাকবে না’ নীতি বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক কাঠামোতে সংস্কার প্রয়োজন।
বর্তমান বাস্তবতায় বাংলাদেশ একটি কেন্দ্রীয়কৃত প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়, যেখানে রাষ্ট্রীয় সেবা ও সুযোগ অনেকাংশেই রাজনৈতিক আনুগত্য, দলীয় পরিচয় কিংবা সামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল। এই ব্যবস্থায় বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ, আদিবাসী জনগণ, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কিংবা তৃতীয় লিঙ্গের জনগণ প্রান্তিক হয়ে পড়ে।
এমনকি শহুরে দরিদ্র জনগণ বা দিনমজুর শ্রেণির মানুষেরা নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকেন। নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় তাদের উপস্থিতি এখনো সীমিত। তরুণ সমাজ—যারা সংখ্যায় বড় ও শক্তিশালী—তাদেরও নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ কম।
উদাহরণস্বরূপ, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণ বা হাওর অঞ্চলের জনগোষ্ঠী এখনো জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত নয়। এই জনগোষ্ঠীগুলোর জন্য যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো গৃহীত হয়, সেগুলো অনেক সময় তাদের পরামর্শ বা অংশগ্রহণ ছাড়াই গৃহীত হয়, যা প্রকৃত অন্তর্ভুক্তির পরিপন্থী। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গৃহহীন হয়ে পড়া বহু জনগণ শহরে এসে বস্তিতে আশ্রয় নিচ্ছে, কিন্তু তারা মৌলিক সেবার সুযোগ পাচ্ছে না—এটিও অন্তর্ভুক্তিহীনতা তৈরি করছে।
অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল হওয়া এবং মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে বসবাসকারী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সহযোগিতা এবং মানবতাবোধ জাগ্রত করা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ নিশ্চিত করতে অপরিহার্য ভূমিকা রাখে, কারণ এটি সমাজে ঐক্য, সমতা এবং অভিন্ন দায়িত্ব গড়ে তোলে।
একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজে বিভিন্ন আদর্শ ও ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আগত মানুষদের সমান সুযোগ এবং সম্মান দেওয়া হয়। এটি কেবল তখনই সম্ভব, যখন বিভিন্ন গোষ্ঠী সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে মানবতাবাদী মূল্যবোধ নিয়ে একসাথে কাজ করে।
উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ আফ্রিকার দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধ পরবর্তী আফ্রিকান জাতীয় পুনর্মিলন প্রক্রিয়া, যা ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশনের (Truth and Reconciliation Commission-TRC) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, সেখানে বিভিন্ন জাতিগত এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করেছিল।
এই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং মানব মর্যাদার ভিত্তিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় গভীর সামাজিক বিভেদ দূর করতে সক্ষম হয়েছিল, যা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের পথ প্রশস্ত করে। এই উদাহরণটি প্রমাণ করে যে, সহযোগিতা এবং মানবিক মূল্যবোধের মাধ্যমে একটি সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব।
মানবতাবাদ প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্যকে গুরুত্ব দেয়, যা প্রান্তিক জনগণকে সমাজে অন্তর্ভুক্তির জন্য এবং নীতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সহায়ক। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) একত্রিত দেশগুলোর একটি মডেল হিসেবে কাজ করছে, যেখানে বিভিন্ন জাতি একসাথে মানবাধিকার, গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখছে।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)-এর সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর জন্য উপকার বয়ে আনছে, যেমন শরণার্থী এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য এটি অনেক সুবিধা নিশ্চিত করেছে। ২০২১ সালে, EU শরণার্থী সংকট মোকাবিলায় সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রেখেছিল, যেখানে শরণার্থীদের জন্য মানবিক সহায়তা প্রদান এবং তাদের মানবাধিকার রক্ষা করা হয়েছে, যা EU-এর মানবিক মূল্যবোধের একটি প্রমাণ।
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং মানবতাবাদ শরণার্থী অধিকার এবং জলবায়ু ন্যায়বিচারের মতো ইস্যুগুলোর সমাধানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জাতিসংঘ এবং এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনগুলো একসাথে কাজ করে বিশ্বের প্রান্তিক জনগণের মৌলিক সুবিধা যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং সহিংসতা থেকে সুরক্ষা প্রদান করছে।
উদাহরণস্বরূপ, United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR (জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা) ২০১৫ সালের শরণার্থী সংকটের সময় মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকা থেকে পালানো শরণার্থীদের সাহায্য করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তারা আশ্রয়, চিকিৎসা সেবা, খাদ্য সহায়তা এবং শিক্ষা প্রদান করেছে, যা মানবিক সহানুভূতি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি উদাহরণ।
সর্বশেষ বিষয় হলো, বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হলে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়—প্রয়োজন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, যেখানে সব শ্রেণি, জাতি, লিঙ্গ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ সমান মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করে। এজন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রশাসনিক সংস্কার, সুশাসন ও মানবিক মূল্যবোধের চর্চা।
ড. মো. রফিকুল ইসলাম ।। অধ্যাপক, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আপনার মতামত দিন:
(মন্তব্য পাঠকের একান্ত ব্যক্তিগত। এর জন্য সম্পাদক দায়ী নন।)